আমাদের আব্বাসউদ্দীন। সুখবিলাস বর্মা।
আমাদের আব্বাসউদ্দীন
সুখবিলাস বর্মা
পঙ্কজকুমার মল্লিক স্মৃতিচারণায় তাঁকে 'অপ্রতিদ্বন্দী পল্লীগীতিশিল্পী'
হিসেবে উল্লেখ করেছেন। হেমাঙ্গ বিশ্বাস তাঁকে 'বাংলার অমর লোকশিল্পী' নামে অভিহিত করেছেন।
পল্লীকবি জসিমউদ্দীন তাঁর নাম দিয়েছিলেন 'অঞ্জনা তীরে খঞ্জনা পাখী, তাঁর সবচেয়ে প্রিয়জনের
কাছে তিনি 'গানের পাখি' ।তিনি বাংলার লোক সংগীতের যাদুকর আব্বাসউদ্দীন আহমেদ। পঙ্কজকুমার
মল্লিক 'আমার যুগ আমার গান'-এ মন্তব্য করেছেন, "সে যুগের প্রখ্যাত পল্লীগীতি বিশারদ
আব্বাসউদ্দীন আহমদ মহাশয়ের কথা একবার স্মরণ করা কর্তব্য মনে করি। … সঙ্গীত জীবনের বিভিন্ন
ক্ষেত্রে তাঁর সংস্পর্শে এসে প্রচুর আনন্দ পেয়েছি। বাংলার লোকগীতির জন্য উৎসর্গীকৃত
প্রাণ ছিলেন তিনি। দেশ বিভাগের কিছু পরে তিনি যখন অন্য দিকে চলে যান তখন মর্মান্তিক
কষ্ট পেয়েছিলাম।"
কখনকার কথা বলছি? কে ছিলেন তিনি, কোথাকার মানুষ-কোন অন্য দিকে
যান তিনি? এসব কথার উত্তর খুব কমই জানেন আজকের মানুষ। তাই এই লেখার উদ্যোগ।
দেশ বিভাগের অর্থাৎ বাংলা ও পাঞ্জাবকে দ্বিখণ্ডিত করে স্বাধীন
ভারতের পতাকা ওড়ে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট। ঢাকায় পাকিস্তানের পতাকা ওড়ে একদিন আগে ১৪ই
আগস্ট । সেদিন ঢাকায় উপস্থিত ছিলেন আব্বাসউদ্দিন। তাঁর নিজের কথায়, 'এলাম ঢাকায়। এক
অপরিচিত পারিপার্শ্বিকে। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট, শবেবরাতের রাত। রাত ঠিক বারোটার পর
ঢাকা রেডিওতে প্রথম কোরানের আয়াত গম্ভীর সুরে আবৃত্তি করলেন এক মওলানা।এর পরই আমার
সৌভাগ্য হোল পাকিস্তানের রেডিওতে প্রথম পাকিস্তানের গান গাওয়ার।' (কথাঃ গোলাম মোস্তফা, সুরঃ আব্বাসউদ্দিন)
সকল দেশের চেয়ে পিয়ারা দুনিয়াতে ভাই
সে কোন স্থান?
পাকিস্তান সে পাকিস্তান ।
… … …
জানো কি ভাই এই দুনিয়ার ফিরদউস তোমার সে কোন খান?
পাকিস্তান সে পাকিস্তান ।
আব্বাসের কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় চলে যাওয়াতে অর্থাৎ দেশ ছেড়ে যাওয়াতে
শুধু পঙ্কজ মল্লিক নন, কলকাতার সংগীত সাহিত্য জগতের বিশিষ্টজন সহ এপার বাংলার, বিশেষ
করে উত্তরবাংলার কৃষক মজুর আপামর জন 'মর্মান্তিক কষ্ট' পেয়েছিলেন। তাঁদের এই কষ্ট ও
তজ্জনিত অভিমানের প্রকাশ আমরা স্বচক্ষে দেখেছি ১৯৯০ সালে 'আব্বাসউদ্দীন স্মরণ সমিতি'
গঠনের পর ।কোচবিহারে সমিতির প্রথম অনুষ্ঠানে আমরা কোচবিহার
এলাকার সব বয়স্ক ভাওইয়া শিল্পীদেরকে সম্বর্ধনা জানিয়েছিলাম। সম্বর্ধনা সভায় বক্তব্য
রাখতে গিয়ে প্রত্যেকেই তাঁদের সেই মনঃকষ্টের কথা তুলে ধরেছিলেন। কয়েকজন আবার আমার বিরুদ্ধে
অভিযোগ করেছিলেন, কেন আমি এমন ব্যক্তিকে স্মরণীয় করার জন্য সংস্থা তৈরি করেছি যিনি
কোনও কারণ ছাড়াই আমাদের দেশ ত্যাগ করেছেন-কোচবিহার ত্যাগ করেছেন ।
আসলে কোচবিহারের মানুষ আব্বাসউদ্দিন ও তাঁর পরিবারকে ভীষণ ভালবাসেন।
তিনি জন্মেছিলেন তৎকালীন দেশীয় রাজ্য কোচবিহারের একটি ছোট্ট গ্রাম বলরামপুরে ১৯০১ সালের
২৭শে অক্টোবর। লেখাপড়া করেছেন গ্রামের স্কুল, তারপর মহকুমা শহর তুফানগঞ্জ স্কুলে। কোচবিহারের
বিখ্যাত ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে আই এ পাশ করেছেন কিন্তু বি এ পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে পারেন
নি পরীক্ষার সময়ে বাবার কঠিন অসুখের কারণে।
সুতরাং জীবনের শৈশব থেকে যৌবনের একটা সময় পর্যন্ত তাঁর কাটে
বলরামপুর, তুফানগঞ্জ ও কোচবিহারে। এই সময়ে লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে গানের চর্চা চলতে থাকে।
কিভাবে চলেছে তাঁর সংগীত চর্চা-ভাওইয়া চর্চা, কার কাছে শিখেছিলেন সেসব গান? এ ধরণের
প্রশ্নের উত্তরে আব্বাসউদ্দিনের গ্রামের আর এক প্রতিভা প্রখ্যাত ভাওইয়া শিল্পী তাঁর
অনুজপ্রতিম প্যারিমোহন দাসের সাবলীল উত্তর "গ্রামের মানুষ এ-গান কারুর কাছ থেকে
ধরাধরি করে শেখে না, শুনে শুনে আপনা-আপনিই শেখে। উঠতে বসতে মাঠে ঘাটে এ-গান শোনা যায়।
যার কণ্ঠে সুর রয়েছে এবং শোনার ইচ্ছে রয়েছে তারা শুনে শুনেই শিখে যায়। প্রাকৃতিক নিয়মে,
প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবে ভাওইয়া চটকার সুর আপনা-আপনিই গলায় বসে যায়" ।
এটাই স্বভাবসিদ্ধ, এটাই রীতি। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের কাছে এটাই
'লোকসংগীতের বাহিরানা'। কিন্তু অনায়াসলব্ধ এই ভাওইয়ার কণ্ঠ সম্পদে আব্বাস সন্তুষ্ট
থাকার মানুষ নন। আরও মহত্তর কিছুর জন্য তাঁর মন উদগ্রীব। চেয়েছিলেন বেনারসে গিয়ে সংগীতে
পাঠ নিতে-পিতার অনুমতি মেলেনি। কোচবিহার শহরে এক বন্ধুর সাহচর্যে দু'একবার সুযোগ হয়েছিল
সরকারী উকিল উচ্চাঙ্গ সংগীত গায়ক রাজেন রায়-এর বৈঠকখানায় ক্লাসিকাল সংগীত শোনার-সেখানেই
সুযোগ হয়েছিল জলপাইগুড়ির (বৈকুণ্ঠপুরের) রায়কত রাজবংশের প্রতিভাধর উচ্চাঙ্গ সংগীত গায়ক
সরোজ রায়কতের গান শোনার। এ সবের মধ্য দিয়ে সংগীতের প্রতি আকুলতা আরও বেড়ে যায়। কলেজে
অর্থনীতির অধ্যাপক চুনিলাল মুখার্জি তাঁকে বার বার উৎসাহ দিয়েছেন কলকাতায় গানের জগতের
অনুসন্ধানে। তাই তাঁর মন চলে যায় কলকাতায় ।
ঠিক এই সময়ে তাঁর জীবনে আসে মহাসুযোগ। কলেজের মিলাদ অনুষ্ঠানে
আমন্ত্রিত হয়ে আসেন কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি আব্বাসের গান শুনে মুগ্ধ হলেন। আব্বাসকে
বললেন কলকাতা আসতে-গান রেকর্ড করার ব্যবস্থা হবে। সুযোগ এলো কলকাতা যাওয়ার-বন্ধু জিতেন
মৈত্রের বিয়ে উপলক্ষে। জিতেন মৈত্র তখন কলকাতায় আইন পড়ছিলেন। যোগাযোগ হোল গ্রামোফোন
কোম্পানির বিমল দাসগুপ্তের সঙ্গে এবং তাঁর সহায়তায় এইচ এম ভি থেকে প্রথম রেকর্ড বের
হল আধুনিক গানের-কবি শৈলেন রায়ের লেখা দু'খানি গান 'কোন বিরহীর নয়ন জলে' এবং 'স্মরণ
পারের ওগো প্রিয়'। প্রথমটির সুরকার গীতিকার ও আব্বাস উদ্দিন, দ্বিতীয়টির সুর ধীরেন
দাসের। গানের কথার উচ্চারণ ঠিক করে দিয়েছিলেন সে সময়কার বিখ্যাত গায়ক কে মল্লিক ওরফে
কাশেম মল্লিক । সালটা ছিল ১৯৩০। বাড়ীর কাউকে না বলেই এসেছিলেন কলকাতা। কণ্ঠগুণে প্রথম
প্রচেষ্টাতেই কিস্তিমাত। ফিরে গেছেন বলরামপুরে। রেকর্ড করা গান সংগীত জগতে যথাযোগ্য
আদর পেয়েছে। আব্বাস আবার কলকাতা এলেন ১৯৩১ সালে। এবারে লক্ষ্য একটি দুটি গান রেকর্ড
করে বাড়ী ফিরে যাওয়া নয়, বাংলা গানের জগতের সুলুকসন্ধান করে নিজেকে এই জগতে প্রতিষ্ঠা
করা। সেবারেও করলেন শৈলেন রায় ও জিতেন মৈত্রের লেখা দু'খানা আধুনিক গানের রেকর্ড। আইন
কলেজের পুনর্মিলন উৎসবে জিতেন মৈত্রের উদ্যোগে সুযোগ পেলেন ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট
হলে সংগীত পরিবেশনের এবং তাঁর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করলেন।এই অনুষ্ঠানের সফলতার মাধ্যমে
স্কটিশচার্চ কলেজ, প্রেসিডেন্সী কলেজ, ওন হোস্টেল, বেকার হোস্টেল, কারমাইকেল হোস্টেল,
বালিগঞ্জ, শ্যামনগর, ডায়মন্ডহারবার, হাওড়া, হুগলী প্রভৃতি নানা স্থান থেকে এলো সংগীত
পরিবেশনের সুযোগ । আব্বাস হয়ে উঠলেন আধুনিক গানের এক সার্থক শিল্পী। থাকেন কলকাতায়
প্রখ্যাত আইনজীবি তসকিন আহমেদের বাড়ীতে-কয়েকটি ছেলেমেয়েকে পড়ানোর বিনিময়ে থাকা খাওয়ার
ব্যবস্থায়। এই সময়ে তিনি গ্রামোফোন কোম্পানি ছাড়াও টুইন, মেগাফোন, রিগ্যাল থেকে রেকর্ড
করেন আধুনিক ছাড়াও পল্লী অঞ্চল থেকে সংগৃহীত ভাটিয়ালি, জারি, সারি, দেহতত্ত্ব, বিচ্ছেদী
ইত্যাদি নানা আঙ্গিকের গান। এ ছাড়াও তাঁর ভাণ্ডারে ছিল নজরুল ও জসীমউদ্দিনের লেখা ভাটিয়ালি
ও অন্যান্য পল্লীসঙ্গীত। ইতিমধ্যে গ্রামোফোন কোম্পানির চিৎপুরের রিহার্সাল রুমে কাজী
সাহেবের সঙ্গে দেখা করে এসেছেন। তিনি আব্বাসকে যথারীতি সাহায্য করে চলেছেন। তাঁরই পরামর্শে
আব্বাস ঠুংরির বাদশা ওস্তাদ জমিরুদ্দিন খাঁ-এর কাছে নাড়া বেঁধে কণ্ঠচর্চা করছেন।
কলকাতায় ও আশেপাশে দু' একটি অনুষ্ঠানে যা পান তাতে তো চলছেনা-তিনি
তো বলরামপুরের বাড়ীতে তাঁর স্ত্রীকে রেখে এসেছেন। সেখানে কেমন আছেন তিনি? সে আর এক
জীবন কাহিনী এক মহিয়সী নারীর, আব্বাস পত্নী লুৎফুন্নেসা বেগমের, যার সঙ্গে শিল্পীর
বিয়ে হয়েছিল ১৯২৯ সালে। এখানে সে আলোচনার সুযোগ নেই। কিন্তু শিল্পীর তো অর্থ সংস্থান
প্রয়োজন। নিজের খরচ বাদেও বাড়ীতে স্ত্রীর কাছে পাঠাতে হবে। তাই তিনি দেখা করলেন তখনকার
ডি পি আই-এর পি এ জলপাইগুড়ির সফিকুল ইসলামের সঙ্গে; তিনিই ঐ অফিসে মাসিক ৪৫ টাকা বেতনে
একটি চাকরি জোগার করে দিলেন। সেখান থেকে যোগদান করলেন বাংলা সরকারের কৃষি বিভাগে স্থায়ী
পদে। এই পদে তিনি কাজ করেছিলেন দীর্ঘ বারো বছর। অফিসে কাজ করছেন, গান চর্চা করছেন,
পরের পর রেকর্ড করে যাচ্ছেন-কিন্তু মন তো পড়ে আছে বলরামপুরে, তুফানগঞ্জে ও কোচবিহারে
যেখানে রয়েছে তাঁর পরিবার-বাবা মা স্ত্রী পুত্র কন্যা। তিন মাস চার মাস পর বা কোন পরব
উপলক্ষে বাড়ী যেতেন। গানের জন্য তাঁদেরকে দীর্ঘ বিরহের জীবন কাটাতে হত। বেগম সাহেবাকে
লেখা শিল্পীর চিঠিগুলো এবং উত্তরে শিল্পীকে লেখা বেগম সাহেবার চিঠিগুলো পড়লে বোঝা যায়
তাঁদের বিরহের মর্ম ও ইতিহাস। এর মধ্যেই তাঁদের জীবনে এসেছে গভীর শোক; তাঁদের দ্বিতীয়
পুত্রকে বাঁচাতে পারেন নি। দুই পুত্র ও এক কন্যা নিয়ে কঠিন জীবন কাটাতেন বেগম সাহেবা।
ক্বচিৎ কখনো তাঁদেরকে কলকাতা এনে রাখতেন মাত্র কয়েকদিনের জন্য। তাই আব্বাসউদ্দিনের
সংসার জীবন অবিচ্ছিন্ন ছিল না কলকাতায়। আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে স্ত্রী পুত্র কন্যা
নিয়ে একনাগাড়ে বাস করতে পারেন নি। বাবার আর্থিক অবস্থা বেশ ভাল ছিল কিন্তু বাবার কাছে
কখনো হাত পাতেন নি। তিনি থাকতেন কোন মেস বা হোটেল-এ। বেগম সাহেবাকে লেখা চিঠিগুলোয়
উল্লিখিত ঠিকানা থেকে দেখা যায় যে তিনি থাকতেন ১২৬, লোয়ার সার্কুলার রোড, ১২১/বি, বহুবাজার
স্ট্রীট, ২৭, শশীভূষণ দে স্ট্রীট, হোটেল স্যাভয় ইত্যাদি জায়গায়। স্ত্রী-সন্তানদেরকে
যখন নিয়ে আসতেন তখন নতুন করে বাড়ী ভাড়া নিতে হতো। তাই কলকাতায় তাঁর ঠিকানা অনেক- পার্ক
সার্কাস, পার্ক স্ট্রীট, ফিয়ারস লেন, কড়েয়া রোড, আহিরিপুকুর, বেনিয়াপুকুর, ধাঙ্গড় বাজার,
বউবাজার ইত্যাদি ।
কলকাতাই তাঁর কাছে সবটুকু। সংগীত জীবনের স্ফুরণ থেকে মধ্য গগন
পর্যন্ত দীর্ঘ বিশ বছরের বেশী সময় কেটেছে তাঁর কলকাতায় । কলকাতা তাঁকে সব দিয়েছে। বড়
সাধ ছিল বেতারে গান গাইবেন-সে সাধও পূর্ণ হয়েছে কলকাতায়। তিনি বলছেন, 'প্রথম যেদিন
রেডিওতে গান গাই সেদিন আমার শিল্পী জীবনে নাতুন এক অনুভুতির স্বাদ পেলাম। … রেডিওতে
গাইতে পারলাম এই তো ভাগ্যি। কতজনে হয়ত আমার গলার সুর কানের ভিতর ধরেছে। এই তো চরম পুরস্কার'
।কলকাতাতেই তিনি সান্নিধ্য লাভ করেছেন তাঁর প্রধান গীতিকার, সুহৃদ, friend
philosopher guide কাজী নজরুল ইসলামের; পেয়েছেন পল্লীকবি জসীমউদ্দিন ও গোলাম মোস্তফার
মতো কবি গীতিকারের সহৃদয়তা। কাজী সাহেবের লেখা ভাটিয়ালি ও ইসলামী সংগীত, পল্লীকবির
লেখা ও সংগৃহীত ভাটিয়ালি ও বিচ্ছেদী, গোলাম মোস্তফার লেখা ইসলামী সংগীত মাধ্যমেই তাঁর
মধুঝরা কণ্ঠ পৌঁছায় বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে।
আব্বাস উদ্দিনের সঙ্গীতজীবনের একটি বড় অধ্যায় জুড়ে রয়েছে বিভিন্ন
রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান করার অভিজ্ঞতা। সভাগায়ক পরিচিতি তাঁর সংগীত জীবনকে
দিয়েছে অন্য মাত্রা। সভা-সমিতিতে গান করতে গিয়েই পরিচিতি ঘটেছে শেরে বাংলা সুরাওরদি-নাজিমুদ্দিন,
মৌলানা আক্রম খাঁ, তুষার কান্তি ঘোষ, সৈয়দ বদ্রুদ্দজা, হুমায়ুন কবীর, তামিজউদ্দিন খান-র
মতো বহু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে। ফজলুল হক তো ছিলেন তাঁর গানের একনিষ্ঠ ভক্ত।
এক সভায় গান শুনে তিনি আব্বাসকে মিলাদে দাওয়াত করলেন। আব্বাস তখন থাকতেন বেনিয়াপুকুর
লেন-এ। মিলাদ শেষে মোল্লারা উঠে দাঁড়ালেন-হক সাহেব একটি হারমোনিয়াম এনে আব্বাসকে মিলাদ
পড়তে বললেন। হারমোনিয়াম বাজিয়ে মিলাদ-এ তো নতুন ধারণা! মোল্লারা সহ্য করতে না পেরে
প্রস্থানের প্রস্তুতি নিয়েছেন। হক সাহেবের অনুরোধে আব্বাসউদ্দিন গান ধরলেন-'তোরা দেখে
যা আমিনা মায়ের কোলে, মধু পূর্ণিমারই সেথা চাঁদ দোলে'। কি আশ্চর্য! মোল্লারা ফিরে এসে
বসে পড়লেন গান শুনতে। আব্বাস ধরলেন, 'জাগে না সে জোশ লয়ে আর মুসলমান, করিল জয় যে তেজ
লয়ে দুনিয়া জাহান'। হক সাহেব কেঁদে চলেছেন-মোল্লাদের মুখে আনন্দের হাসি। হক সাহেবের
সৌজন্যেই চাকরি পেয়েছিলেন শিল্পীর জন্যই সৃষ্ট Recording Expert to the Govt. of
Bengal পদে ।
গানের সুবাদে থিয়েটার ও সিনেমার সঙ্গেও যোগাযোগ ঘটেছিল। নাট্যাচার্য
শিশির কুমার ভাদুরী মঞ্চে তাঁকে দিয়ে 'আমার গহীন গাঙের নাইয়া' গানটি করিয়েছিলেন। নাট্যাচার্য
তাঁকে 'সীতা' ছবিতে বৈতালিকের পার্ট দেবেন ঠিক করেছিলেন, কিন্তু ছবির প্রযোজক কোন মুসলমানকে
নেওয়াতে আপত্তি জানিয়েছিলেন। হিন্দু নাম নিয়ে অভিনয় করার প্রস্তাবে রাজি হন নি আব্বাস
। এরপর আব্বাস জ্যোতিষ বন্দোপাধ্যায়ের 'বিষ্ণুমায়া', তুলসি লাহিড়ীর 'ঠিকাদার' ছবিতে
অভিনয় করেন। 'ঠিকাদার' ছবির শুটিং হয়েছিল দমনপুর ষ্টেশনের কাছে এক চা বাগানে। এছাড়াও
'মহানিশা' ও 'একটি কথা' ছবিতেও অভিনয় করেছিলেন।
এ সবকিছুই ঘটেছে কলকাতাকে ঘিরে। তাঁর জীবনে নাম যশ অর্থ প্রতিপত্তি
সবই প্রায় কলকাতা ভিত্তিক। সবই পশ্চিমবঙ্গ ভিত্তিক। হ্যাঁ, কলকাতা তাঁর একটি বাসনা পূর্ণ করে নি, প্রধানত তাঁর নিজের দোষেই।
তিনি কবিগুরুকে গান শোনাতে পারেন নি। কাজী সাহেবের ইচ্ছে ছিল রবীন্দ্রনাথকে আব্বাসের
গান শোনানোর। কিন্ত এড়িয়ে চলার অভ্যাসের জন্য সম্ভব হয় নি। কাজী সাহেবের উদ্যোগ, প্রতি
বারেই কোনও না কোনও অজুহাতে, আব্বাস এড়িয়ে গেছেন ।


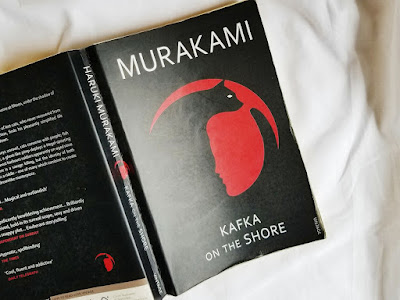

অসাধারণ এক লেখা।বেশ ভালো লাগলো।ধন্যবাদ এমন একটি যুগোপযোগী লেখার জন্য ♥️
ReplyDelete